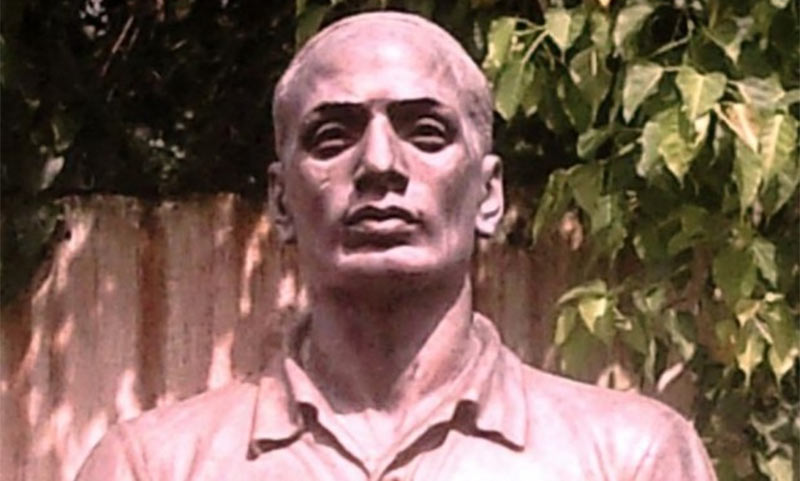বিবেকানন্দ মোহন্ত
“An Advocate of violence in its extreme forms and a notoriously dangerous Leader of the Terrorist Parties.” (তথ্যসূত্র ১)
পুলিশের গোপন ডায়েরিতে বিশের দশকের প্রথমেই যে কথাগুলো লেখা হয়েছিল অগ্নিযুগের যে বিপ্লবীর উদ্দেশ্যে, সেই মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেনের পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বরাক উপত্যকায় উপস্থিতি এবং বছরখানেকের মতো এখানে অবস্থানের বিষয়টি এই অঞ্চলবাসীদের কাছে নিশ্চিতরূপেই অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। বস্তুতপক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা সংগঠন তরুণ সংঘ, অনুশীলন সমিতি, শ্রীসংঘ, যুগান্তর দল, এমনকি সূর্যসেন পরিচালিত ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির ( IRA) সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল এই উপত্যকার বিপ্লববাদ। এজাতীয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ডাক লুট, ব্যাঙ্ক লুট সহ রাজনৈতিক ডাকাতি ইত্যাদি, যেগুলো সংঘটিত হয়েছিল সুরমা-বরাকের একাধিক স্থানে। এমনকি ঐতিহাসিক দেওঘর মামলা থেকেও দূরে থাকেননি বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব – যাঁদের সাথে ছিল মাস্টারদার অন্তরঙ্গতা এবং স্বস্নেহ সাহচর্য। এইসব বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ রেখাপাত করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা।
এক:-
এই আলোচনার শুরুতেই আমাদের একটু দৃকপাত করতে হবে তৎকালীন ছোট্ট শহর করিমগঞ্জের বিপ্লববাদী চিন্তাধারার বিষয়ে। আমরা জানি যে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সঞ্জাত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অর্থাৎ National Council of Education ( NCE)-এর অন্তর্গত দুই-দুইটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সিলেট ও হবিগঞ্জে। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল (5th Standard ) দুটি ব্রিটিশের রোষানলে পড়ে বন্ধ করতে হয়েছিল ১৯১২ -‘১৩ সালে (হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় প্রধান মহেন্দ্রনাথ দে’র উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর)। পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রদীক্ষিত ঐসব স্কুলের প্রাক্তনীদের নিয়ে সিলেট জাতীয় বিদ্যালয় প্রধান শ্রীশচন্দ্র দত্ত করিমগঞ্জ চলে আসেন এবং বহুজাতিক সংস্থা সমান্তরালে গড়ে তুলেন The Karimganj Tea Association; নবগঠিত এই সংস্থার অধীনে তখন গড়ে ওঠেছিল একাধিক চা-বাগান, যার মধ্যে অন্যতম হল কৈলাশহরের নিকটবর্তী ‘দি কালীশাসন টি কোম্পানি লিমিটেড’। এখানে উল্লেখ্য যে, কালীশাসন চা-বাগানটির প্রথম স্বত্বাধিকারী ছিলেন ‘দেবীযুদ্ধ’ প্রণেতা কবি শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর পরই এটির মধ্যে জাতীয়তাবাদের গন্ধ দেখতে পেয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন এবং অচিরেই গ্রন্থটিকে কালো তালিকাভুক্ত করে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।
যাইহোক শ্রীশচন্দ্র দত্ত শরচ্চন্দ্রের সাথে পরামর্শ করে বাংলার বিপ্লবীদের কালীশাসন চা-বাগানে রাখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বিপ্লবী বাঘা যতীন ( যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ) এবং তাঁর সহযোগীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠেছিল এই চা-বাগান। এঁদের সহযোগিতায় সেসময় স্বাধীন ত্রিপুরায় একটি বিপ্লবী অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল শ্রীশচন্দ্রের, কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ তারিখে ঊড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীমোহনার বালাসোর উপকূলে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বাঘা যতীন সহ অনেকেরই মৃত্যু ঘটেছিল। প্রসঙ্গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলার বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রবোঝাই জার্মান জাহাজ বালাসোর উপকূলে নোঙ্গর ফেলেছিল এবং সেই অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব পড়েছিল বাঘা যতীনদের উপর।
অনুমান করা যায় যে, কালীশাসন চা-বাগানে বিপ্লবী অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা, এবং বাঘা যতীন ও তাঁর সহযোগীদের সেখানে রাখার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে সেদিনের ছোট্ট শহর করিমগঞ্জের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। আমার এরূপ ধারণা এই কারণেই যে, ১৯১৩ সালে জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর পরই শ্রীশদত্ত এবং তাঁর অনুগামী সিলেট-হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় প্রাক্তনীদের ক’জন পাকাপাকিভাবে করিমগঞ্জ চলে এসেছিলেন। এবং গড়ে তুলেছিলেন Karimganj Tea Association সহ অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শিল্পসংস্থা। সেই সুবাদে বাঘা যতীন ও তাঁর সহযোগী বিপ্লবীরা সম্ভবত করিমগঞ্জ এসে সাময়িক অবস্থান করেছিলেন এবং কালীশাসনে বিপ্লবী অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে পরিকল্পনা করেছিলেন।
দুই :-
মাস্টারদা সূর্যসেনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার প্রেক্ষাপট :
বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন বহরমপুরের যুগান্তর দলের কর্মী বিপ্লবী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট থেকে। সতীশচন্দ্র তাঁকে শোনালেন আয়ারল্যান্ডের ইস্টার বিদ্রোহের কথা। মুক্তিপাগল হাজার হাজার আইরিশ তরুণ যেমন সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন,”Be it for the Defence or be it for the assertion of a national liberty, I look upon the sword as a sacred weapon.” তরবারি আমার পবিত্র অস্ত্র, স্বাধীনতার জন্য আমি তা হাতে তুলে নিলাম। মাস্টারদা সতীশচন্দ্রের কাছ থেকে শুনেছিলেন বাঘা যতীনের কথাও। যতীন বলতেন, “None but the brave/ None but the brave / None but the brave / Deserves the Fair.” আটারো বছর বয়সের তরুণ সূর্যসেন এবার খুঁজে পেলেন বেঁচে থাকার মন্ত্র,” শৃঙ্খল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাক, নব আন্দোলনে গড়ে উঠুক নতুন জীবন”। ১৯১৮ সালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বহরমপুর কলেজের পাঠ সমাপনান্তে সূর্যসেন চলে এসেছিলেন জন্মস্থান চট্টগ্রামে, এবং গণিতের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন স্থানীয় উমাতারা হাইস্কুলে। সেদিন থেকে তাঁর পরিচিতি হল মাস্টারদা হিসেবে। এই অভিধা নিয়ে ভাবনা শুরু করলেন যে, চট্টগ্রামে এমন একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যার দাপটে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠে। সেই চিন্তাধারা থেকেই ১৯১৮ সালে চারজন বিপ্লবী যথাক্রমে অনুরূপচন্দ্র সেন,নগেন্দ্রনাথ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং চারুবিকাশ দত্তকে নিয়ে গড়ে তুলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি। এঁদের সাথে এসে যোগ দেন আরও সাতজন তরুণ তুর্কি, তাঁরা হলেন – নির্মল সেন, নন্দলাল সিংহ, প্রমোদ চৌধুরী, আসরাফুদ্দিন, অবনী ভট্টাচার্য, অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষ। এই দলে যোগ দেন লোকনাথ বল সহ আরও অনেক কিশোর-তরুণেরা। মাস্টারদার সুযোগ্য নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটলো চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরেও।
গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনেও মাস্টারদা ও তাঁর সহযোগীরা যোগদান করেছিলেন। ঐপর্বে ১৯২১ সালে তদানীন্তন করিমগঞ্জ মহকুমার চরগোলাভ্যালি চা-বাগান থেকে উৎসারিত মুলুক চলো আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। সেসময় চাঁদপুর স্টেশনে অবস্থানরত শিশু-যুবা-বৃদ্ধ/বৃদ্ধা সহ হাজার হাজার নিরীহ চা-শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রের বর্বরোচিত আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার খবর চাঁদপুর অতিক্রম করে চট্টগ্রাম সহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অকূস্থলে ছুটে এসেছিলেন চাঁদপুরের হরদয়াল নাগ, চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সস্ত্রীক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজ সহ সুরমা-বরাকের মানবদরদী সুধী জনসাধারণ। চা-শ্রমিকদের এই মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন ও তাঁর সংগ্রামী সদস্যরা। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনখ্যাত বিপ্লবী অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, চারুবিকাশ দত্ত সহ আরও অনেকেই। সুতরাং দেখা যায়, মুলুক চলো আন্দোলনের সূত্র ধরে চাঁদপুর-চট্টগ্রাম-বরাক উপত্যকার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল সেই ১৯২১ সালের অসহযোগ পর্ব থেকেই।
তিন :-
বরাক উপত্যকায় মাস্টারদা সূর্যসেনের আগমন ও বিপ্লবী কর্মতৎপরতা :
বরাক উপত্যকায় মাস্টারদাকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন হাইলাকান্দির তরুণ বিপ্লবী উপেন্দ্র কুমার ধর। তাঁর আদি বাড়ি ছিল পঞ্চখণ্ডে এবং পিতা ব্যবসায়িক সূত্রে হাইলাকান্দিতে বসবাস করছিলেন। উপেন্দ্রবাবুও বাল্যকাল থেকে পিতার সাথে হাইলাকান্দিতেই ছিলেন। পড়াশোনা করতেন স্থানীয় সরকারি বিদ্যালয়ে। ১৯২১-২২ সাল থেকে যখন কাটাখাল-লালাবাজার রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছিল, তখন হাইলাকান্দিতে রেলদপ্তরের একটি কার্যালয় গড়ে ওঠেছিল যেখানে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে আগত রাজেন দাস। তিনি ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের মন্ত্রশিষ্য এবং যুগান্তর দলের একজন একনিষ্ঠ সদস্য। রেলকর্মী রাজেন দাসের সাথে হাইলাকান্দির খেলার মাঠে পরিচয় হয় উপেন্দ্র ধরের। ক্রমে এই পরিচয় হৃদ্যতায় পর্যবসিত হয় এবং তিনিও শ্রীদাসের সংস্পর্শে এসে যুগান্তর দলের বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। একইভাবে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন উপেন্দ্র ধরের এক ক্লাশ সিনিয়র গজেন ভাদুড়িও। ১৯২৩ সালে রাজেন দাস চট্টগ্রামে বদলী হয়ে গেলে উপত্যকার বিপ্লবী সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন উপেন্দ্র ধর। পরবর্তীতে রাজেন দাসের পিতৃশ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন উপেন্দ্র ধর। সেখানে থাকাকালীন মাস্টারদার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই কাজে পাঁচ/ছয়দিন তিনি মাস্টারদার বাড়িতেও গিয়েছিলেন। এই যোগাযোগের মধ্য দিয়েই বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা এবং আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করে হাইলাকান্দিতে ফিরে এসেছিলেন উপেন্দ্রবাবু।
এই ঘটনার কিছুদিন পর ১৯২৩ সালের ২৬ ডিসেম্বরে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সতেরো হাজার টাকা ডাকাতি করা হয়েছিল মাস্টারদার নেতৃত্বে। কিন্তু ‘সুলুকবাহার’ নামীয় আস্তানায় আত্মগোপনরত মাস্টারদা এবং সহযোগীদের সাথে ব্রিটিশ পুলিশের সংঘর্ষে মাস্টারদা এবং অম্বিকা চক্রবর্তী আহত ও বন্দী হন। অবশিষ্ট বিপ্লবীরা পালাতে সক্ষম হলেও অনন্ত সিংহ ধরা পড়ে যান। বিচার প্রক্রিয়াকালীন সময়ে চট্টগ্রাম আদালতে বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে জোর সওয়াল করেছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। শেষপর্যন্ত সূর্যসেন ও সহযোগীরা আদালত থেকে ছাড়া পেলেও ব্রিটিশ পুলিশ-প্রশাসন কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। আবার ধরপাকড় শুরু করে, ফলে অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রমুখেরা পুনরায় গ্রেফতার হন। মাস্টারদা পুলিশের চোখ এড়িয়ে কলকাতায় গেলেও পুলিশ তাঁর পিছু ছাড়েনি। পুলিশের চোখে ভয়ঙ্কর এই বিপ্লবী নেতা ক্রমাগত আস্তানা পাল্টাতে পাল্টাতে একসময় বরাক উপত্যকায় চলে আসেন, সেটা ১৯২৪ সালের শেষদিকের কথা।
প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব চঞ্চল শর্মার মতে ১৯২৪ সালের বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে অনেক বিপ্লবী গ্রেফতার হন এবং মাস্টারদা আত্মগোপন করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মগোপন করে চট্টগ্রামে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ায় উপেন্দ্রবাবু (হাইলাকান্দির উপেন্দ্র ধর) ১৯২৪ সালের শেষদিকে তাঁকে হাইলাকান্দিতে নিয়ে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯২৪ সালে হাইলাকান্দি থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে উপেন্দ্রবাবু চট্টগ্রামে চলে যান ডাক্তারী পড়ার জন্য। কিন্তু বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করার ফলে তাঁর ডাক্তারী পড়া আর শেষ হয়ে ওঠেনি।
যাইহোক, মাস্টারদা সূর্যসেন বরাক উপত্যকায় এসে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে থেকেছিলেন ১৯২৫ সালের শেষ অবধি। করিমগঞ্জ প্রবাস জীবনে তিনি থাকতেন সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ, অকৃতদার অবনী লাহিড়ীর বাসায়। শ্রীলাহিড়ী ছিলেন করিমগঞ্জ বিপ্লবী সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা এবং তাঁর বাড়িটি ছিল যুগান্তর দলের প্রধান কেন্দ্র। অপরদিকে হাইলাকান্দিতে অবস্থানকালীন সময়ে মাস্টারদা থাকতেন উপেন্দ্রবাবুদের বাসায়। চঞ্চল শর্মা লিখছেন,” সূর্যসেনের উপস্থিতির ফলে ঐ অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজ বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়”। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত Political History of Assam, Vol-2 (1920-39) গ্রন্থের মতে,”In 1925, Surya Sen and Rajen Das, the famous Bengal Terrorists and the Leaders of the Chittagong Yugantar Party took shelter at Karimganj while evading arrest under the Bengal Criminal Law Amendment Act. with the help of Tarakishore Bardhan, Yosoda Chakraborty, Aboni Lahiri, Upen Dhar, Luxmi Buxi and Umashankar Patua. The group tried to organize the Yugantar network at Hailakandi, Silchar, Habiganj and throughout Sylhet District”.
এখানে উল্লেখ্য যে, মাস্টারদা এবং উপরোক্ত অন্যান্য বিপ্লবীদের অধিকাংশই ছিলেন চট্টগ্রাম, কুমিল্লা সহ সংলগ্ন এলাকার বিপ্লবী ছিলেন। উমাশঙ্কর পাটোয়া ছিলেন শিলচরের, অবনী লাহিড়ী করিমগঞ্জের এবং উপেন্দ্র ধর হাইলাকান্দির অধিবাসী। সূর্যসেন করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি কিংবা শিলচরে অবস্থান করলেও তাঁদের কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র যে শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল – এমনটা না ও তো হতে পারে, প্রয়োজনে তাঁরা অনুশীলনের তাগিদে গ্রামাঞ্চল কিংবা সন্নিহিত পাহাড়ি অঞ্চলেও গিয়ে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় এওলাবাড়ি চা-বাগানের কথা। এই বাগানের ম্যানেজার ছিলেন স্বদেশী হরিপদ দত্ত এবং কম্পাউন্ডার ছিলেন ক্ষীরোদ মোহন ভট্টাচার্য। ১৯৩৩ সালের ১৩ মার্চ বছর কুড়ির তরুণ বিপ্লবী অসিত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ইতিহাসখ্যাত ইটাখলা রেলস্টেশনে ডা
কলুট হয়েছিল এবং ব্রিটিশের বিচারে ২জুলাই ১৯৩৪ তারিখে কুড়ি বছর বয়সী তরুণ তুর্কি অসিত ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়েছিল সিলেট কারাগারে। এই মহান বিপ্লবী অসিত ভট্টাচার্যের পিতা ছিলেন এওলাবাড়ি চা-বাগানের কম্পাউন্ডার ক্ষীরোদমোহন ভট্টাচার্য। অপরদিকে অসিত ভট্টাচার্যের অগ্রজভ্রাতা বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ছিলেন মাস্টারদার যুগান্তর ও ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির (IRA) এক বিপ্লবী যোদ্ধা। তিনি ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালের ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনে সামিল হয়েছিলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে তিনদিন পর অর্থাৎ ২২ এপ্রিল তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ব্রিটিশ বাহিনীর ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং তার বিপরীতে বিপ্লবীদের মধ্যে এগারোজন শহিদ হয়েছিলেন। সেই এগারোজনের মধ্যে ছিলেন বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
সুতরাং অনুমিত হয় যে, করিমগঞ্জ অবস্থানকালীন সময়ে বিধুভূষণের সাথে যোগাযোগ ঘটেছিল মাস্টারদা সূর্যসেনের। এবং সেই সূত্র ধরেই হয়তো পৈত্রিক কর্মস্থল এওলাবাড়ির নিভৃত পার্বত্য পরিসরে বিপ্লবী অনুশীলন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, কর্মতৎপরতা কিংবা নিয়মিত মহড়াপর্বও চলতো।
যাইহোক মাস্টারদা বরাক উপত্যকায় বছরখানেক অবস্থান করে যুগান্তর দলের কর্মসংস্কৃতির কার্যসম্পাদন করে উত্তরভারতীয় বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার সাথে পরিচিত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এবং এখানে আসামাত্রই ১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর পুলিশের হাতে বন্দী হলেন দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার সূত্রে। পরবতীতে ১৯২৮ সালে এখান থেকে প্যারোলে ছাড়া পেয়ে চলে আসেন চট্টগ্রামে এবং প্রতিষ্ঠা করলেন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (আইআরএ)-র চট্টগ্রাম শাখা। নবগঠিত এই সংগঠনের সর্বাধিনায়ক হন মাস্টারদা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ।
অপরদিকে মাস্টারদা সূর্যসেনের মন্ত্রশিষ্য উপেন্দ্র কুমার ধর পরবর্তী সময়ে এলাহাবাদ চলে যান এবং ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকরি নিয়ে কানপুরে অবস্থান করেন, কিন্তু বিপ্লবী কর্মতৎপরতা থেকে দূরে সরে যাননি। এই পর্বে ১৯২৬ সালে এলাহাবাদ ত্রিবেণীতে এক গোপন সভায় মিলিত হন শহীদ ভগৎ সিংয়ের সাথে। এবং তাঁর প্রেরণায়া দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে চাকরি ছেড়ে কুমিল্লার অভয়াশ্রমে এসে যোগ দেন।আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয় তাঁদের বিপ্লবী কর্মতৎপরতা।এরই সূত্র ধরে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে খুন, জখম, ডাকাতি ও অস্ত্র-আইন ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ১৯২৮ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের দায়রা আদালতের বিচারে ১২ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাইলাকান্দির উপেন্দ্র কুমার ধর এবং সুশীল সেন।বিচারে অন্য অনেকের তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের কারাদণ্ড হলেও সাত বছরের সর্বোচ্চ কারাদণ্ডে যে দু’জন দণ্ডিত হন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাইলাকান্দির উপেন্দ্র কুমার ধর।
শেষকথা :-
আজ ৭৭তম স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে দাঁড়িয়ে শতাধিক বছর আগের ছোট্ট শহর করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর সহ সুরমাভ্যালির তদানীন্তন অখ্যাত শহর-গঞ্জ-গ্রামাঞ্চলের জনগণের কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় ততটুকু অগ্রসর না হওয়া সত্বেও তৎকালীন যুবপ্রজন্ম দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে এগিয়ে আসতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তাইতো তাঁরা পরিবার-পরিজনের স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করে দেশের জন্য শহিদ হতে পেরেছিলেন। বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেনের নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে চলা এরূপ অকুতোভয় সেনানীদের মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এক সময় ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভবপর হয়ে ওঠেছিল। আজ স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে সেদিনের মহানায়ক এবং সহস্র মহাপ্রাণ বিপ্লবী ব্যক্তিবর্গদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম।
তথ্যসূত্র:-
১) প্রবন্ধ :- বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন ও চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ: একটি পুনরবলোকন, বিকাশ রঞ্জন দেব, অনীক, মে, ২০২৩।
২) চরগোলা এক্সোডাস ১৯২১, বিবেকানন্দ মোহন্ত।
৩) শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন, স্মৃতিকথা, চঞ্চল শর্মা।
৪) স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্ট-কাছাড়, নিশীথ রঞ্জন দাস।
৫) শ্রীহট্ট পরিচয়, রণেন্দ্রনাথ দেব, ডিসেম্বর ১৯৮৩।
৬) Political History of Assam, Vol-2(1920-’39), Ed- A. C. Bhuiya & Sibapada Dey, Govt. of Assam, 1st edn.,1978.